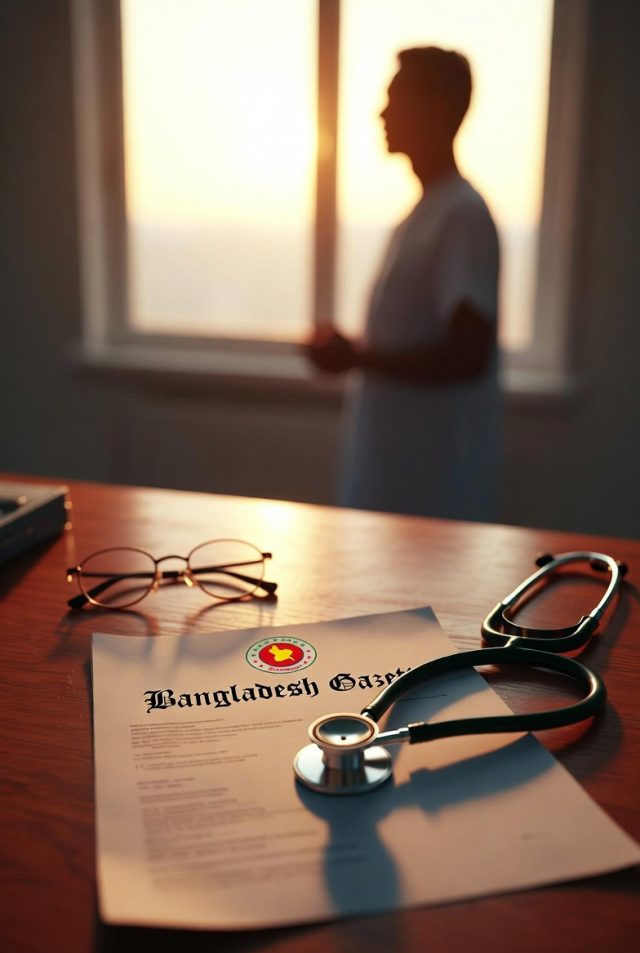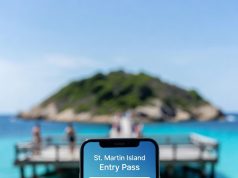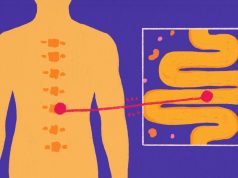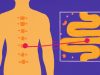নতুন আইনের আলোয় জীবন ও জীবিকা: অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সাতকাহন
পর্ব-১
আমিরুল মোমেনিন, ঢাকা: দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে বাংলাদেশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে যে আইনি জটিলতা রোগীদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা অবশেষে দূর হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা ‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে ১৯৯৯ সালের পুরনো আইনটি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকায়ন এবং মানবিক প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি নতুন এই আইনটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন—পুরনো আইনের সাথে নতুন আইনের মূল পার্থক্য কোথায়? কেনই বা পুরনো আইনটি বাতিল করতে হলো?
‘নিকট আত্মীয়’: বৃত্তের পরিধি বাড়ল বহুগুণ
১৯৯৯ সালের আইনে অঙ্গদাতার সংজ্ঞা ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। কেবল পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এবং স্বামী-স্ত্রী—এই গুটিকয় সম্পর্কের মধ্যেই অঙ্গদান সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে হাজার হাজার রোগী দাতা খুঁজে পেতেন না। এমনকি পরিবারে ইচ্ছুক দাতা (যেমন চাচাতো ভাই বা মামা) থাকা সত্ত্বেও আইনি বাঁধায় তারা অঙ্গ দান করতে পারতেন না।
২০২৫-এর নতুন অধ্যাদেশের ২(৭) ধারায় ‘নিকট আত্মীয়’-এর সংজ্ঞায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে পূর্বের সম্পর্কের পাশাপাশি রক্ত-সম্পর্কিত আপন চাচা, ফুফু, মামা, খালা, নানা, নানি, দাদা, দাদি, নাতি, নাতনি এবং খালাতো, মামাতো, ফুপাতো ও চাচাতো ভাই-বোন এমনকি ভাতিজা-ভাতিজি ও ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং সৎ ভাই-বোনও আইনগতভাবে অঙ্গদান করতে পারবেন।
এই একটি পরিবর্তন হাজার হাজার রোগীকে বিদেশমুখী হওয়া থেকে আটকাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ইমোশনাল ডোনার ও সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্ট: মানবিকতার আইনি স্বীকৃতি
পুরনো আইনে রক্তের সম্পর্কের বাইরে গিয়ে অঙ্গদানের কোনো সুযোগ ছিল না, যা অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ডেকে আনত। নতুন আইনের ২(৮) ধারায় ‘ইমোশনাল ডোনার’ বা নিঃস্বার্থবাদী দাতার ধারণা যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মীয়তা নেই কিন্তু দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক বা ভালোবাসার টানে কেউ চাইলে মেডিকেল বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে অঙ্গ দান করতে পারবেন।
এছাড়া, ‘সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্ট’ বা অদলবদল পদ্ধতির বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ধরুন, ‘ক’ রোগীর দাতা আছে কিন্তু ব্লাড গ্রুপ মিলছে না, আবার ‘খ’ রোগীরও একই সমস্যা। সেক্ষেত্রে ‘ক’-এর দাতা ‘খ’-কে এবং ‘খ’-এর দাতা ‘ক’-কে অঙ্গ দিতে পারবেন। ১৯৯৯ সালের আইনে এই আধুনিক পদ্ধতির কোনো স্থান ছিল না।
ব্রেইন ডেথ ও ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টের স্পষ্ট রূপরেখা
১৯৯৯ সালের আইনে ‘ব্রেইন ডেথ’ বা মস্তিষ্কের মৃত্যু নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল, ফলে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ (ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট) বাংলাদেশে কখনোই জনপ্রিয় হয়নি। নতুন আইনের ৬নং ধারায় ব্রেইন ডেথ ঘোষণার জন্য সুস্পষ্ট প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছে। মেডিসিন, নিউরোলজি ও অ্যানেসথেসিওলজি—এই তিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে কমিটি ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করবে। এটি বাংলাদেশে মরণোত্তর অঙ্গদানের পথ সুগম করবে।
বিদেশ নির্ভরতা ও অর্থ পাচার রোধ
কিডনি বা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ রোগী ভারত, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডে পাড়ি জমান। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দেশে বৈধ দাতার অভাব।
রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের কিডনি রোগ বিভাগের প্রধান বলেন, “আমার এমন অনেক রোগী ছিলেন যাদের কাজিন (cousin) কিডনি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ৯৯-এর আইনের কারণে আমরা নিতে পারিনি। চোখের সামনে রোগীগুলো জমি বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেছে। নতুন আইনে চাচাতো-মামাতো ভাইবোন বা ইমোশনাল ডোনার বৈধ হওয়ায় এখন দেশেই স্বল্প খরচে এই চিকিৎসা সম্ভব হবে, বাঁচবে বৈদেশিক মুদ্রা।”
কেস স্টাডি: আইনি জটে আটকে ছিল সুমনের জীবন
৩৫ বছর বয়সী ব্যাংক কর্মকর্তা সুমন (ছদ্মনাম) গত দুই বছর ধরে কিডনি বিকল হয়ে ডায়ালাইসিস নিচ্ছিলেন। তার আপন ভাই বা বোন নেই। তার মামাতো ভাই তাকে কিডনি দিতে চাইলেও পুরনো আইনের কারণে তা সম্ভব হয়নি। আইনি জটিলতায় হতাশ সুমন যখন সব আশা ছেড়ে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই এল ২০২৫-এর এই নতুন অধ্যাদেশ। সুমনের মামাতো ভাই এখন আইনত বৈধ দাতা। সুমন বলেন, “এই আইনটা আরও ৫ বছর আগে হলে হয়তো আমার মতো হাজার হাজার রোগীকে এত কষ্ট পেতে হতো না।”
‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ কেবল একটি আইনি দলিল নয়, এটি মুমূর্ষু রোগীদের জন্য বাঁচার নতুন সনদ। আত্মীয়তার সংজ্ঞা প্রসারণ এবং মানবিক দাতাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এই আইন চিকিৎসার বাণিজ্যিকীকরণ রোধে এবং দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাইলফলক হয়ে থাকবে।